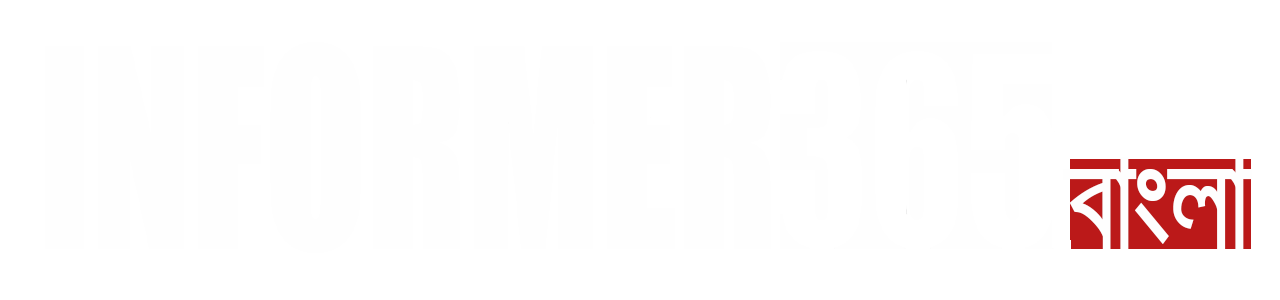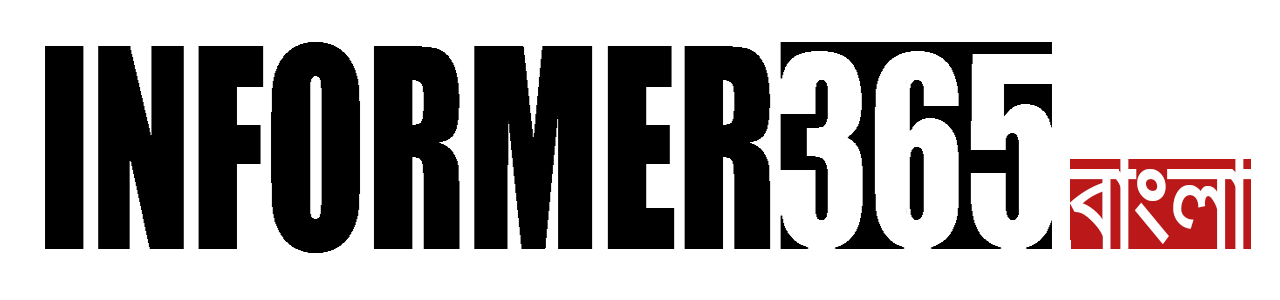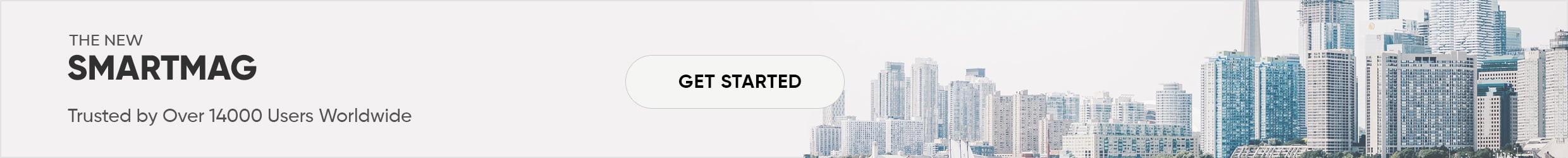বিশ্ব অর্থনীতিতে গত এক দশকে অভূতপূর্ব পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। শিল্পোন্নত পশ্চিমা দেশগুলোর অর্থনৈতিক আধিপত্য ক্রমশ কমে আসছে। এর বিপরীতে, এশিয়া, লাতিন আমেরিকা এবং আফ্রিকার উদীয়মান অর্থনীতির দেশগুলো বৈশ্বিক অর্থনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে উঠে আসছে। অর্থনীতিবিদরা এই পরিবর্তনকে “গ্লোবাল ইকোনমিক শিফট” হিসেবে অভিহিত করেছেন। এটি শুধু একটি অর্থনৈতিক স্থানান্তর নয়; এর প্রভাব বৈশ্বিক রাজনীতি, সংস্কৃতি এবং সামাজিক কাঠামোতেও পড়ছে।
১৯৫০ থেকে ১৯৮০ সাল পর্যন্ত, উত্তর আমেরিকা এবং ইউরোপ বিশ্ব অর্থনীতির প্রায় ৭০ শতাংশ নিয়ন্ত্রণ করত। যুক্তরাষ্ট্র ছিল বৈশ্বিক জিডিপির শীর্ষে এবং এটি প্রযুক্তি, সামরিক শক্তি এবং আর্থিক খাতে অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিল। তবে ১৯৯০-এর দশকের শেষ থেকে উদীয়মান অর্থনীতির দেশগুলো দ্রুতগতিতে এগিয়ে আসতে শুরু করে। চীন এবং ভারতের মতো দেশগুলো উৎপাদন, বাণিজ্য এবং প্রযুক্তিতে নিজেদের শক্তি বৃদ্ধি করে। ২০২৩ সালে প্রকাশিত বিশ্বব্যাংকের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বৈশ্বিক অর্থনীতিতে উন্নত দেশগুলোর অংশীদারিত্ব হ্রাস পেয়ে ৪৫ শতাংশে এসেছে। বিপরীতে, উদীয়মান দেশগুলোর অংশীদারিত্ব ৩৫ শতাংশ অতিক্রম করেছে।
এই পরিবর্তনের প্রধান কারণগুলোর মধ্যে একটি হলো উন্নত দেশগুলোতে জনসংখ্যায় বার্ধক্যের আধিক্য এবং শ্রমবাজার সংকোচন। উদাহরণস্বরূপ, জাপান এবং ইউরোপের বেশ কয়েকটি দেশে জন্মহার উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে। এতে উৎপাদনশীলতা হ্রাস পেয়েছে এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ধীর হয়েছে। অন্যদিকে, উদীয়মান অর্থনীতির দেশগুলোতে তরুণ জনসংখ্যা এবং সস্তা শ্রমশক্তি উৎপাদন এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে গতি এনেছে। চীনের উদাহরণটি এখানে প্রাসঙ্গিক। ১৯৭৮ সালে অর্থনৈতিক সংস্কারের পর থেকে চীন তার উৎপাদন শিল্পে বিপ্লব ঘটিয়েছে। আজ, এটি বিশ্বের বৃহত্তম রপ্তানিকারক এবং দ্বিতীয় বৃহত্তম অর্থনীতি।
বাণিজ্য উদারীকরণ এবং প্রযুক্তির অগ্রগতিও এই পরিবর্তনের বড় কারণ। ১৯৯০-এর দশকে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (ডব্লিউটিও)-এর প্রতিষ্ঠা উদীয়মান দেশগুলোকে বৈশ্বিক বাজারে নিজেদের অবস্থান শক্তিশালী করার সুযোগ সৃষ্টি করে। পাশাপাশি, ই-কমার্স এবং ডিজিটাল অর্থনীতির উত্থান উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য নতুন সুযোগ সৃষ্টি করে।
এই পরিবর্তন কিছু গুরুতর চ্যালেঞ্জও এনেছে। উদীয়মান অর্থনীতির দেশগুলোতে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি সত্ত্বেও সম্পদের অসম বণ্টন বিদ্যমান রয়েছে। চীনে শহুরে অঞ্চলের উন্নতি সত্ত্বেও গ্রামীণ এলাকায় দরিদ্রতা রয়ে গেছে। অন্যদিকে, উন্নত দেশগুলোর অর্থনৈতিক শ্লথগতির কারণে তাদের জনগণের জীবনযাত্রার মান হ্রাস পেয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রে ২০২২ সালে বেকারত্বের হার বেড়ে ৬ শতাংশে পৌঁছায়।
বিশ্ব অর্থনীতির এই পরিবর্তন আন্তর্জাতিক রাজনীতিতেও প্রভাব ফেলছে। চীন তার বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভ (বিআরআই) এর মাধ্যমে এশিয়া, আফ্রিকা এবং ইউরোপে বিনিয়োগ বাড়াচ্ছে। এর মাধ্যমে এটি তার ভূরাজনৈতিক প্রভাব বাড়াচ্ছে। অন্যদিকে, ব্রিকস (ব্রাজিল, রাশিয়া, ভারত, চীন এবং দক্ষিণ আফ্রিকা) গোষ্ঠী উদীয়মান দেশগুলোর জন্য একটি বিকল্প মঞ্চ হিসেবে কাজ করছে। এই পরিবর্তনগুলো পশ্চিমা দেশগুলোর জন্য চ্যালেঞ্জ তৈরি করছে। উদাহরণস্বরূপ, যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপীয় ইউনিয়ন তাদের অর্থনৈতিক এবং কৌশলগত প্রভাব ধরে রাখতে নতুন নতুন নীতি গ্রহণ করছে।
বিশ্ব অর্থনীতির এই পরিবর্তনের ভবিষ্যৎ নির্ভর করবে স্থানীয় এবং বৈশ্বিক নীতিমালার উপর। উদীয়মান অর্থনীতির দেশগুলোকে অবশ্যই টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে হবে। এটি নিশ্চিত করতে তাদের উচিত শিক্ষা এবং প্রযুক্তিতে বিনিয়োগ বাড়ানো। একইসঙ্গে, উন্নত দেশগুলোকে উদীয়মান দেশগুলোর সঙ্গে সহযোগিতা বাড়াতে হবে। পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তির উদ্ভাবন এবং কার্বন নিঃসরণ কমানোতে একত্রে কাজ করা জরুরি।
বিশ্ব অর্থনীতির এই স্থানান্তর বৈশ্বিক ক্ষমতার একটি নতুন বিন্যাস তৈরি করছে। এটি বিশ্বকে নতুন সুযোগ এনে দিতে পারে। সঠিক সিদ্ধান্ত এবং কার্যকর নীতিমালা ছাড়া এই পরিবর্তন গভীর বৈষম্য এবং সংকট সৃষ্টি করতে পারে। অর্থনীতির পুনর্বিন্যাসে লাভবান হতে হলে সব দেশকেই সমন্বিতভাবে কাজ করতে হবে।